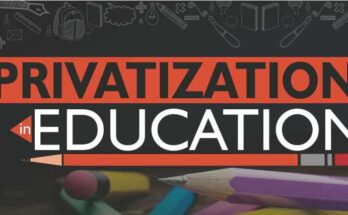শুভ্রদীপ ঘোষ
সহজিয়া মূদ্রণ: নভেম্বর, ২০২২, শারদ সংখ্যা

সময়টা গত শতকের ৮০ দশকের শেষ, প্রাক উদারীকরণ যুগ। দূরদর্শনের জাতীয় চ্যানেলে যশপাল ভাট্টি নামের এক কৌতুকাভিনেতার পরিচালনায় ‘ফ্লপ শো’ নামের একটি ধারাবাহিক সম্প্রচার হত। ডার্ক কমেডি গোত্রের এই অনুষ্ঠানে কৌতুকের মোড়কে বিভিন্ন জ্বলন্ত ইস্যুকে পরিবেশন করা হত, চালু ব্যবস্থার নানা অযৌক্তিকতাকে সূক্ষ্ম ভাবে তুলে আনা হত আমাদের বসার ঘরে। এই অনুষ্ঠানের একটি পর্বের শিরোনাম ছিল ‘পিএইচ ডি স্কলার’। সেই পর্বে আমরা দেখেছিলাম, এক পিএইচ ডি গাইডকে যিনি তাঁর তুলনায় দুর্বল ছাত্রকে দিয়ে বাড়ির যাবতীয় কাজ করিয়ে নিচ্ছেন, তার কাজে সময় দিচ্ছেন না, ছাত্রীর সাথে আলোচনার সময় তার কাজের চেয়ে বেশি নজর দিচ্ছেন তার চেহারা, পোশাক-আশাকের দিকে। ডার্ক কমেডির দাবি মেনেই সেই পর্বে এসেছিল আরও একটি ঘটনা। সেই গাইড তাঁর শ্যালিকার জন্য উপযুক্ত পাত্রের সন্ধানে বেরিয়ে পাকড়াও করেছিলেন তাঁর কাছে কাজ প্রায় শেষ করে ফেলা তুলনায় কাবিল একটি ছাত্রকে। কিন্তু যখন জানতে পারলেন, তার বাগদান হয়ে গিয়েছে তখন কেন তাঁকে জানানো হয়নি, এই মর্মে চোটপাট করে তার শেষ হয়ে যাওয়া কাজের সমালোচনা করে হুকুম দিলেন, আরও কাজ করে আনতে হবে, নয়তো তার থিসিসে সই করা যাবে না। এ দিকে তুলনায় দুর্বল ছাত্রটিকে সম্ভাব্য পাত্র ধরে নিয়ে তাকে যত্ন-আত্তির নামে কাবিল ছাত্রটির কাজ নকল করে তিন বছরে থিসিস করিয়ে ডিগ্রি পাইয়ে দিলেন।
পিএইচ ডি বস্তুটি এবং তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জুড়ে থাকা গাইড-স্কলার সম্পর্কের জটিলতা নিয়ে কোনও ধারণা যখন তৈরি হয়নি, তখন ‘ফ্লপ শো’-এর এই পর্বটি অনেকাংশেই বাড়াবাড়ি মনে হত। ৯০ দশকের মাঝামাঝি নিজে যখন পিএইচ ডি করার কথা ভাবছি, তখন দক্ষিণ কলকাতার এক শতাব্দী-প্রাচীন প্রতিষ্ঠানে এক গাইডের গল্প শুনলাম। শুনলাম, তাঁর সঙ্গে কাজ করা স্কলারদের উপর নির্দেশ আছে বিয়ে করতে গেলে তাঁর অনুমতি নিতে হবে। তা না হলে উনি অসন্তুষ্ট হবেন এবং থিসিসে সই করবেন না। সেই বিজ্ঞানী এই ধরনের মানসিক উৎপীড়নে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। পরিচিত এক বন্ধু তিন বছরে পিএইচ ডি শেষ হবে এবং যথেষ্ট সংখ্যক ভাল মানের গবেষণাপত্র হবে এই ইতিহাস জেনে উৎসাহিত হয়ে ওঁর সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে মাঝপথে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। কারণ দিনের পর দিন তুচ্ছ তুচ্ছ বিষয়ে যন্ত্রণা পেতে পেতে তার আত্মবিশ্বাস তলানিতে গিয়ে ঠেকছিল। এই ধরনের ঘটনা জানার পর ‘ফ্লপ শো’কে অতিরঞ্জিত ভাবতে পারিনি। কিন্তু এর মানে এটাও নয় যে, সার্বিক ভাবে পিএইচ ডি গাইড গোষ্ঠীটি সম্বন্ধে কোনও নেতিবাচক ধারণা তৈরি হয়েছিল। আমার নিজের গাইড ছিলেন সম্পূর্ণ অন্য ধরনের মানুষ। ছাত্রের শারীরিক, মানসিক স্থিতি তাঁর কাছে সবসময়েই প্রাধান্য পেত। উনি কোনও ব্যতিক্রমী চরিত্র ছিলেন না। আশেপাশে বহু বরিষ্ঠ অধ্যাপক গবেষকদের মধ্যে এই দায়িত্ব এবং মমত্ববোধ দেখেছি। অল্প কিছু উদাহরণ ছিলেন, যাঁরা ছাত্রদের সঙ্গে চূড়ান্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ করতেন এবং তাদের অসহায়তার পূর্ণ সুযোগ নিতেন। সেই সময়ে বুঝতে শুরু করি ‘ফ্লপ শো’ আসলে সমাজের নানা দিকের নেতিবাচক দিকগুলির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করানোর দায়িত্ব পালন করছিল, যাতে ক্ষমতার অসাম্য এবং তার খারাপ দিকগুলি সম্বন্ধে আমরা ওয়াকিবহাল থাকি, গোটা ব্যবস্থাটা সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব তৈরি করার জন্য নয়।
৯০ দশকে আর্থিক উদারীকরণের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবিত্তের উচ্চাকাঙ্ক্ষায় এল ঈগলের উড়ান। উচ্চশিক্ষা বিশেষত গবেষণা জগতেও তার ছায়া পড়ল। অনেকেই আশা করেছিলেন, শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্র-শিক্ষক সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কেও বইবে উদারতার হাওয়া, বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করার সুযোগ এবং উৎসাহী গবেষকদের আর্থিক সামর্থ্যে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন আসবে গবেষকদের মানসিক কাঠামোতেও, শিক্ষাজগতে পশ্চিমের দেশগুলির আপাত খোলামেলা পরিবেশ, গবেষক ছাত্র এবং শিক্ষকের মধ্যে আপাত সাম্যের সম্পর্কের ছায়া পড়বে বিদেশ ফেরত ভারতীয়দের দৃষ্টিভঙ্গিতে, বিশেষত তাঁরা যখন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে গবেষক শিক্ষক হবেন। উদারীকরণের তিন দশক পার হয়ে গিয়ে ছবিটা কি সত্যিই তাই না কি ‘ফ্লপ শো’ যা দেখিয়েছিল, সেটাই এখনও প্রবল ভাবে বিরাজমান? এমনকি শিক্ষকতা গবেষণায় ইন্সটিটিউট অফ এমিনেন্সের তকমা পাওয়া এলিট প্রতিষ্ঠানগুলিতেও?
নির্মোহ দৃষ্টিতে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে দেখা যাবে ছবিটা বিশেষ বদলায়নি। তিন দশকে উপরের প্রলেপ সরিয়ে দিলেই পলেস্তারা খসে প্রাচীন কাঠামোটি বেরিয়ে পড়বে। এক একটা ঘটনা এই প্রলেপ সরানোর কাজে অনুঘটকের কাজ করে, যেমনটা হয়েছিল এই বছরের শুরুর দিকে একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের কৃতী গবেষকের আত্মহত্যার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে। এই ঘটনাটা বিশেষ সাড়া ফেলেছিল দুটি কারণে। প্রথমত, আপাতদৃষ্টিতে ছাত্রটির গবেষণার কাজ ছন্দে চলছিল, কিন্তু যে যন্ত্রণাদায়ক পদ্ধতিতে সে আত্মহত্যা করেছিল এবং আত্মহত্যার নোটে পরিষ্কার ভাষায় তার গাইডকে দায়ী করে গিয়েছিল, তা গোটা গবেষক সমাজকে একটা প্রবল ঝাঁকুনি দিয়েছিল। কারণ প্রচলিত ঘটনার সঙ্গে এই ঘটনাটি একেবারেই মেলানো যাচ্ছিল না। দ্বিতীয়ত, বিশেষত গবেষক ছাত্রদের মধ্যে এই ঘটনার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার তীব্রতা। বিভিন্ন গণমাধ্যমে বন্যার জলের মতো বেরিয়ে পড়েছিল বর্তমান এবং প্রাক্তন ছাত্রদের জমে থাকা ক্ষোভ। সে দিনই পরিষ্কার হয়ে গেছিল, এ দেশের গবেষণা কাঠামোতে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক খুব সুস্থ, খুব স্বস্তিদায়ক জায়গায় নেই। একটু ভাবলেই বোঝা যাচ্ছিল, ‘ফ্লপ শো’ যে প্রবণতাগুলি হাল্কা কৌতুকের ছলে পরিবেশন করেছিল, সেই প্রবণতাগুলির উৎস আসলে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোয়, যে কাঠামোয় ছাত্র-শিক্ষক সমীকরণের অসাম্য ক্রমাগত বেড়েই চলেছে।
প্রায় তিন দশক গবেষণা এবং শিক্ষকতায় কাটানোর সূত্রে টেবিলের দুই প্রান্তেই থাকার সুযোগ হয়েছে। সেই অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, ভারতীয় কাঠামোয় গবেষণার ক্ষেত্রে গাইড-স্কলারের ঊর্ধ্বতন-অধস্তন সম্পর্কই প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে স্বীকৃত। এর মূল কারণ হল, স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত একটি ছাত্রের অনুসন্ধিৎসাকে, প্রশ্নহীন আনুগত্যের পরিবর্তে প্রশ্ন করে যাচাই করে নেওয়ার রেওয়াজকে নীচু নজরে দেখার, বিষয় শেখার বদলে পরীক্ষায় নম্বর পাওয়াকেই মোক্ষ করে দেখানোর ট্র্যাডিশন। স্বাভাবিক ভাবেই গবেষণার জন্য যে মানসিকতা তৈরি হওয়া দরকার, তার সুযোগ প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে থাকে না। এর ফলে যে ছাত্র বা ছাত্রী গবেষণায় আসে, সে অনেকাংশেই নির্ভরশীল হয়ে পড়ে তার গাইডের উপর। ফলে ক্ষমতার সমীকরণে যে সম্পর্কে এমনিতেই যথেষ্ট অসাম্য, তা বেড়েই যায়। শিক্ষার এই সীমাবদ্ধতা সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে বহুলাংশে ক্ষমতাশালী গাইডের উপরে। তাঁরা বুঝতেই পারেন না, কোন জায়গায় সীমারেখা টানা উচিত। তাঁরা বুঝতে পারেন না, অনেক ক্ষেত্রেই গবেষক স্কলারের ‘কনসেন্ট ’ মূল্যহীন, কারণ ‘না’ বলার ফল কোন দিকে গড়াতে পারে, সে সম্পর্কে সে সর্বদাই অনিশ্চিত। প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে গেঁড়ে বসা ক্ষমতার অসাম্যে যে ক্ষমতাহীন, তার অন্য কিছু ভাবার স্বাধীনতা থাকে না। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সাধারণ ভাবে ঘটে চলা কিছু ঘটনার উদাহরণ দিলে বিষয়টা স্পষ্ট হবে।
(১) ল্যাবরেটরির জিনিসপত্র কেনা, বিশেষত পরীক্ষামূলক গবেষণার ক্ষেত্র, একটি আবশ্যিক অঙ্গ। গবেষক স্কলারকে সেই কাজে পরিচিত করাটাও ট্রেনিং এর অংশ, এ নিয়ে কোনও দ্বিমত নেই। প্রশ্ন হল, সীমারেখা নিয়ে। জিনিসপত্র কেনার নানা স্তর আছে। তাতে টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন অর্থাৎ কী মানের জিনিস কেনা হবে, সেটা তৈরি করা, তার পর সম্ভাব্য বিক্রেতাদের কাছ থেকে দরপত্র বা কোটেশন নেওয়া, তার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানের কাছে আবেদনপত্র ( Indent) দেওয়া এগুলি প্রাথমিক কাজ। এর পরের স্তরে থাকবে এই আবেদনের ভিত্তিতে করা বিজ্ঞাপনের উত্তরে যে দরপত্রগুলি আসবে সেগুলি খতিয়ে দেখা, টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশনের সঙ্গে সঙ্গে দামের তুলনামূলক খতিয়ান পরীক্ষা করা এবং তার ভিত্তিতে কার কাছ থেকে জিনিস কেনা হবে সেটা চূড়ান্ত করা। প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রতাকে টপকে কাজটা দ্রুততার সঙ্গে সমাধার জন্য বিভিন্ন প্রশাসনিক বিভাগে খোঁজখবর নেওয়া, প্রয়োজনে ধর্না দেওয়াও পদ্ধতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। প্রাথমিক আবেদন বা Indent পেশের পর এই কাজগুলি বিভাগের অশিক্ষক টেকনিক্যাল কর্মীদের করার কথা, বিশেষত কেন্দ্রীয় অনুদানে চলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে যেখানে এই ধরনের কর্মীদের অভাব নেই। অথচ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অনেক বিভাগেই এই কাজগুলো শুরু থেকে শেষ অবধি সুষ্ঠু ভাবে করার দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হয় গবেষক স্কলারের উপর। অথচ এই করণিক গোত্রের কাজগুলি থেকে তার গবেষণার এক ফোঁটা উপকারও হয় না, কেবল নষ্ট হয় সময়।
(২) বিশেষত কেন্দ্রীয় অনুদানে চলা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে গবেষক স্কলারদের পঠন পাঠনে সহকারী শিক্ষকের ভূমিকা পালন করতে হয়। তাতে কোনও আপত্তি নেই। বরং এই অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতে চাকরি পেতে সহায়ক হতে পারে। সমস্যা হয় যখন প্রতিষ্ঠান বা বিভাগ থেকে তার ভূমিকা নির্দিষ্ট করে দেওয়া থাকে না। এর ফলে সম্ভাবনা থাকে, যে শিক্ষকের সহকারীর ভূমিকায় সে থাকবে, তিনি প্রকারান্তরে ছাত্রটিকে দিয়েই সমস্ত কাজ করিয়ে নেবেন। এই কাজের মধ্যে থাকতে পারে রোজকার ক্লাসে পড়ানোর বিষয়বস্তু বানানো, অ্যাসাইনমেন্ট বা টিউটোরিয়াল তৈরি, তার সমাধান, এমনকি প্রশ্নপত্র তৈরি ও তার সমাধান, পরীক্ষার সমস্ত খাতা দেখা। অর্থাৎ যার সহকারীর ভূমিকায় থেকে শিক্ষানবিশী করার কথা, তাকেই প্রধান ভূমিকায় ঠেলে দেওয়া হচ্ছে, তার নিজের কাজের সময় ব্যয় করে লেগে থাকতে হচ্ছে অতিরিক্ত দায়িত্বে। যথাযথ নির্দেশিকার অভাবে তার অপারগতা জানানোর কোনও জায়গাই থাকছে না।
(৩) অনেক ক্ষেত্রেই এটা দেখা যায় যে, স্কলারের জন্যও গবেষণার কাজ এবং ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে ভারসাম্যের প্রয়োজন, এই সহজ সত্যটি শিক্ষকরা অনুধাবন করেন না। কিছু দিন আগে সামাজিক মাধ্যমে একটি কথোপকথন চলছিল। একজন ছাত্র ভারতে গবেষণার পরিবেশ বিষয়ে মন্তব্য করেছিল যে, এখানে অধ্যাপকরা তাঁদের কাজের নির্ঘণ্ট ছাত্রদের উপর চাপিয়ে দেন। উদাহরণ হিসেবে সে বলেছিল যে, এ দেশে সপ্তাহান্তেও গবেষণার কাজ পুরোদমে চালিয়ে যাওয়াটা ব্যতিক্রম নয়, নিয়ম। এতে দেশের প্রথম সারির এক বৈজ্ঞানিক তাকে উপহাস করে বললেন, ‘‘সপ্তাহান্তে কাজ করতে না চাইলে গবেষণায় আসাই উচিত না।’’ এই মনোভাব ব্যতিক্রমী নয়, বরং এক রকম স্বীকৃত। অন্য সমস্ত ভাল লাগা শিকেয় তুলে কেবল বিষয়ের গবেষণায় মন না দিলে নাকি মোক্ষ লাভ হবে না– এমনটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আনাচে কানাচে কান পাতলেই শোনা যাবে।
গবেষণার মতো সৃষ্টিশীল কাজে মানবিক সম্পর্কের গুরুত্ব সম্পর্কে আমরা চরম উদাসীন। স্বাভাবিক ভাবেই ক্ষমতাহীনের মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়ে নজর দেওয়ার প্রয়োজন ক্ষমতাবানেরা বোধ করেন না। শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্কে সীমারেখা টানার প্রয়োজনীয়তাও স্বভাবতই নেই। পিএইচ ডি গবেষকদের ক্রমবর্ধমান আত্মহত্যার মিছিল নিয়ে খুব কম লোকেরই মাথাব্যথা আছে। উল্টে এমন মত পোষণ করতে দেখেছি, ‘‘আমাদের সময় বাবা এ সব মানসিক সমস্যা-টমস্যা ছিল না’’, ‘‘এ সব ফাঁকিবাজির অজুহাত’’, ‘‘আমরাও তো গবেষণার বাইরে গাইডের এই কাজগুলো করে দিয়েছি। এখন এত আপত্তি কীসের’’। চরিত্রগত ভাবে এই মানসিকতা স্কুলে শৃঙ্খলার নামে শারীরিক নিগ্রহ, কলেজ হোস্টেলে পরিবেশের সাথে মানানসই করার অজুহাতে রযাগিংয়ের সমর্থনের সমতুল্য। সমস্যা যখন চরম আকার ধারণ করে, শেষ হয় আর একটি সম্ভাবনাময় প্রাণ, তখন প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তি মানুষেরা একটু নড়েচড়ে বসেন। কিন্তু সমস্যার মূলে যাওয়ার অনিচ্ছার কারণে শেষ পর্যন্ত ঘুরিয়ে দোষ পড়ে ছাত্রসমাজের উপর। ছাত্রীর উপর যৌন নির্যাতন হলে যেমন ‘‘না বাবা আমার গ্রুপে কোনও মেয়ে নেব না। কখন কোথায় ফেঁসে যাব’’, তেমনই ছাত্রের আত্মহত্যার ঘটনা ঘটলে ‘‘ছাত্রদের তো আজকাল আর কিছু বলাই যাবে না দেখছি। বরং ওদের কাজ আমাদেরই করে দিতে হবে’’—— খুব চেনা প্রতিক্রিয়া। ৮৫ শতাংশ সংখ্যাগুরু গোষ্ঠীর দেশে যেমন ঢুকিয়ে দেওয়া গেছে সংখ্যাগুরুরাই আসলে বিপদগ্রস্ত, গবেষক শিক্ষকদের এক বড় অংশের মনে তেমনি গেঁথে গেছে ক্ষমতাহীন ছাত্রগোষ্ঠীর উৎপীড়নে নাকি তাঁরা বড়ই বিপন্ন।
তা হলে এই অবস্থার সমাধান কী? খুব সহজ রাস্তা না হলেও প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে কিছু উদ্যোগের প্রয়োজন আছে, যেখানে শিক্ষক, ছাত্র দুই পক্ষের অংশগ্রহণ এবং সহযোগিতা জরুরি। একটি উদ্যোগ দীর্ঘমেয়াদী ( bottoms up approach) যাতে স্কুল স্তর থেকে শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্কে পারস্পরিক সম্মান, গণতান্ত্রিক পরিবেশ, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সংবেদনশীলতার চর্চা অবশ্য কর্তব্য। প্রয়োজন এমন পরিবেশ সৃষ্টির, যেখানে ক্ষমতার অসাম্যকে স্বীকৃতি দিয়ে ক্ষমতাশালীর দ্বারা ক্ষমতাহীনের জন্য উপযুক্ত জায়গা ( space) তৈরি করা আবশ্যিক। এই নতুন ট্র্যাডিশন কোনও একক, এমনকি ছোট গোষ্ঠীর উদ্যোগে তৈরি হওয়া ব্যতিক্রমী উদাহরণ হলে চলবে না। এর জন্য তৃণমূল স্তর থেকেই প্রশাসনিক উদ্যোগ প্রয়োজন।
নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়নের প্রেক্ষাপটে দেখলে এই ট্র্যাডিশন তৈরি হওয়া কষ্টকল্পনা। কিন্তু তা বলে হাল ছেড়ে বসে থাকাও কোনও কাজের কথা নয়। সুতরাং, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বল্পমেয়াদী ( top down approach) পরিকল্পনা নেওয়া কিছুটা হলেও বর্তমান অবস্থার সুরাহা করতে পারে। এ জন্য নিম্নলিখিত উদ্যোগগুলি নেওয়া যেতে পারে:
(১) শিক্ষক গবেষকদের জন্য সংবেদনশীলতার পাঠক্রম চালু করে ক্ষমতার অসাম্য সম্বন্ধে তাঁদের অবহিত করা এবং ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কে সীমারেখার সুস্পষ্ট ধারণা তৈরি করা জরুরি। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, কেন্দ্রীয় অনুদানে চলা প্রতিষ্ঠানগুলিতে গবেষণার যন্ত্রপাতি কেনা সংক্রান্ত করণিকের কাজগুলি অশিক্ষক কর্মচারীদের জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া যেতে পারে, যাতে গাইড সেই কাজগুলি ছাত্রের উপর চাপিয়ে না দেন। প্রয়োজনে যথেষ্ট সংখ্যক অশিক্ষক কর্মচারী নিয়োগ করতে হবে। এটি আরও বেশি প্রযোজ্য রাজ্য সরকার পোষিত কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে। এই কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সাধারণত গবেষণাকে নিরুৎসাহিত করা হয়। তা সত্ত্বেও যে শিক্ষকরা গবেষণায় প্রাণপাত করেন, তাঁরা অশিক্ষক কর্মচারীদের কোনও সাহায্য পান না। কারণ একে তো যথেষ্ট সংখ্যক কর্মচারীর অভাব, তার উপর তাঁদেরকে এই কাজে নিয়োজিত করার পরিকল্পনার অনুপস্থিতি। ফলে ছাত্র গবেষকদের উপর অকাজের ভার কমিয়ে তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে চাইলে এই সিদ্ধান্ত আবশ্যক।
শিক্ষকদের সংবেদনশীল করার জন্য প্রথম বিশ্বে এই ধরনের উদ্যোগ চালু আছে। যদিও সাম্প্রতিক গবেষণার ফলাফল জানাচ্ছে সেখানেও শিক্ষক সমাজের মধ্যে এ বিষয়ে উৎসাহের যথেষ্ট অভাব। (সূত্রঃ কানাডার কার্লটন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমীক্ষা: https://www.csit.carleton.ca/~arya/FacultySurveyResults.pdf)
(২) ছাত্রছাত্রীদের মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়ে নিয়মিত যত্ন নেওয়ার উপযুক্ত বন্দোবস্ত করা। এই বিষয়ে কেবলমাত্র কিছু গতানুগতিক ব্যবস্থা চালু না রেখে প্রতিষ্ঠান এবং ডিপার্টমেন্টগুলিতে সমান্তরাল উদ্যোগ নেওয়া জরুরি। সাধারণত প্রতিষ্ঠানে এই বিষয়টি দেখভাল করার জন্য থাকে একটি কমিটি, যার সদস্য হন শিক্ষণপ্রাপ্ত মনোবিদ। নিছক সংখ্যার চাপেই বড় প্রতিষ্ঠানে এই ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়। এ ছাড়া, প্রতিটি ডিপার্টমেন্টের নিজস্ব কিছু সমস্যা থাকে, যেগুলির স্থানীয় স্তরে সমাধান ছাত্রছাত্রীদের পক্ষেও তুলনামূলক ভাবে স্বস্তিদায়ক হতে পারে। সুতরাং দরকার ডিপার্টমেন্টে এমন একটি কমিটি, যাতে প্রতিনিধিত্ব থাকবে শিক্ষক এবং ছাত্র উভয়েরই। এই কমিটি প্রতিষ্ঠানের কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ রেখেই কাজ করতে পারে। এই বিষয়টি সফল হতে হলে শিক্ষক সদস্যদের সংবেদনশীল হওয়া এবং ক্ষমতার সমীকরণের দিকটি সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা জরুরি।
(৩) প্রতিটি পিএইচ ডি গাইডকে তাঁর সঙ্গে কাজ করা ছাত্রদের মানসিকতা বুঝে তাকে সেই মতো ব্যবহার করার অনুশীলন জরুরি। গবেষণা কোনও যান্ত্রিক বিষয় নয়, এর কোনও নির্দিষ্ট ছাঁচ হয় না। পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে ছাত্রকে দিয়ে তার যতটা ক্ষমতা ততটা বের করে নেওয়াটাই গাইডের কাজ। সুতরাং সকলের জন্য এক লক্ষ্যমাত্রা, একই ধরনের নিয়ম-কানুন আখেরে ফলপ্রসূ না-ও হতে পারে। গাইডকে সব সময় এটা মাথায় রাখতে হবে যে, তাঁর তুলনায় ছাত্রটির পরিস্থিতি অনেকটাই অস্থিতিশীল। তাকে কাজ শেষ করতে হবে মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে। কারণ ফেলোশিপের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলে তার অবস্থা প্রায় অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকের মতো। তাই ছাত্রটিকে সফল ভাবে লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়ার কাজে তাঁর পেশাদারি এবং মানবিক সহায়তা ম্যাজিকের কাজ করতে পারে। এই বিষয়ে উদাহরণ ভুরি ভুরি আছে। একই সঙ্গে প্রতিটি ছাত্রের মানসিক স্থিতির দিকে নিয়মিত নজর রাখা, নিজের রিসার্চ গ্রুপের মধ্যে এমন পরিবেশ তৈরি করা যাতে ছাত্র বা ছাত্রী নির্ভয়ে অসম্মতি জানাতে পারে অবস্থার পরিবর্তনে সহায়ক হবে।
(৪) জ্বলন্ত সমস্যাকে চটজলদি কিছু সমাধান দিয়ে ঠান্ডা ঘরে পাঠিয়ে দেওয়ার ধারাবাহিক উদাহরণের ফলে প্রচলিত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাগুলির উপর ছাত্রসমাজের আস্থা ক্রমশ কমে এসেছে। সুতরাং প্রতিষ্ঠানকে উদ্যোগী হতে হবে কাউকে আড়াল করার চেষ্টা না করে পদ্ধতিগত জটিলতার দোহাই দিয়ে সমাধানের সময়সীমা টেনে বাড়ানোর ট্র্যাডিশনকে ভাঙার। প্রশাসনিক পদে আসীন শিক্ষকদের এটা বোঝা দরকার যে প্রতিষ্ঠানের মুখ পোড়ে অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটার কারণে নয়, তার যথাযথ সমাধান না হওয়ার কারণে।
(৫) গবেষক ছাত্রছাত্রীদের দিক থেকে যথেষ্ট উদ্যোগের অভাব এই সমস্যাকে বাড়িয়ে তোলার পিছনে কিছু অংশে দায়ী। দেওয়ালে পিঠ ঠেকার পরিস্থিতি হলে জোটবদ্ধ হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। অথচ এই বিষয়ে গবেষক ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অদ্ভুত স্থিতিজাড্য। এটা ঠিক যে, এই সময়টা তাদের কাছে চরম অসহায়তার। কারণ এই গবেষণার উপর তাদের ভবিষ্যৎ অনেকাংশেই নির্ভরশীল। ফলে ভয়ে, ভক্তিতে তাদের চুপ করিয়ে রাখা কিংবা তাদের ঐক্যের মধ্যে ফাটল ধরানো খুব সহজ। কিন্তু এই কথাটা মনে রাখা দরকার যে , সমস্যার মূল যখন ব্যবস্থার মধ্যে, তখন তার শিকার যে কেউ যে কোনও সময়ে হতে পারে। ফলে দিশাপূর্ণ জোটবদ্ধতা ছাড়া হাল ফেরানোর কোনও সহজ রাস্তা নেই।
‘ফ্লপ শো’তে কৌতুকের আঙ্গিকে দেখানো সমস্যা যে জটিলতায় পৌঁছেছে তার থেকে উদ্ধার পেতে এই স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার সমান্তরাল প্রয়োগ ছাড়া অন্য সমাধানের পথ কোনও ভাবেই চোখে পড়ছে না। প্রচলিত ধারার আমূল সংস্কার ছাড়া সুড়ঙ্গের শেষে আলোর সন্ধান পাওয়ার সম্ভাবনা নেই আর সেই কাজ শুরু করতে হবে এখনই। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে গবেষণায় যুক্ত মানুষদের বিচ্ছিন্নতা যত বাড়বে, ক্ষমতার অসাম্য ততই ফুলেফেঁপে উঠবে। তার ফলে দীর্ঘমেয়াদে যে ক্ষতি হবে, তার ফল ভোগ করতে হবে প্রায় সকলকেই।
পরিশেষে স্বীকার করে নিই, এই লেখা ভীষণ ভাবে পক্ষপাতদুষ্ট। এই লেখা পড়ে সহকর্মীদের অনেকেই রুষ্ট হতে পারেন, মনে করতে পারেন, এই লেখায় ছাত্রদের সাদা এবং শিক্ষকদের কালোয় দেখানো হয়েছে। কেউ কেউ একাধিক উদাহরণ দিতে পারেন যেখানে ছাত্রের দায়িত্ববোধের অভাবের জের মেটাতে হয়েছে তার গাইডকে। সেগুলি বাস্তব হলেও অন্য দিকে পাল্লা এত ভারী যে ভারসাম্য আনা অসম্ভব। যখন সময়মতো ফেলোশিপের টাকা না আসাটা দস্তুর হয়ে দাঁড়ায়, যখন গবেষণার যন্ত্রপাতির উপর অতিরিক্ত কর বসানোর কারণে ছাত্রের কাজ সময়ে শেষ হওয়া অনিশ্চিত হয়ে যায়, যখন কিছু কিছু জায়গায় বিনা ফেলোশিপে এক থেকে দুই বছর কাটানো ব্যতিক্রম গণ্য হয় না কিন্তু বার্ষিক মূল্যায়নে সন্তুষ্টিজনক ফলাফল না হবার দায় একমাত্র ছাত্র বা ছাত্রীর উপর বর্তায়, যার জেরে তার ফেলোশিপের ৫০ থেকে ১০০ শতাংশ কাটা যেতে পারে, যখন যৌন নির্যাতন থেকে শুরু করে অন্যান্য মানসিক নির্যাতনের বিচার আটকে থাকে বছরের পর বছর এবং আমরা শিক্ষক গবেষক সমাজ হয় চুপ থাকি অথবা ঘুরিয়ে দোষ চাপিয়ে দিই ক্ষমতাহীনের উপর, তখন ভারসাম্যের চেষ্টা করাটা ক্ষমতাশালীর অবস্থানকেই শক্তিশালী করা, তার ন্যারেটিভকেই স্বীকৃতি দেওয়া। অর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে সমাধানের রাস্তা খোঁজার বদলে নিজেই সমস্যার অংশ হয়ে যাওয়া।