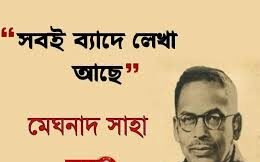(খাদ্যাভ্যাসে দেশভাগের প্রভাব)
শ্রাবন্তী ঘোষাল
তারপর এল সেই দিন।১৪ই আগস্ট,১৯৪৭।ঘড়িতে রাত বারোটা বাজার আগেই ভারতীয় উপমহাদেশের মানচিত্রে পাঞ্জাব-সিন্ধু-গুজরাট-মারাঠা-দ্রাবিড়-উৎকল-বঙ্গ আর গলা জড়াজড়ি করে রইল না।ভাগ্যবিধাতার কলমের খোঁচায় এই পৃথুলা বৃটিশ উপনিবেশ ভেঙে প্রথমে জন্ম নিল পাকিস্তান।আর তার একটু পরেই রাত ১২টা অতিক্রান্ত সময়ে ভারতের জন্ম।যে দেশকে এতদিন মাতৃরূপে কল্পনা করে দেশবাসীকে স্বাধীনতা অর্জনের নেশায় বুঁদ করা হত সেই সাধের মা হলেন ভাগের মা।তাই নিজের জন্মস্থান ছেঁড়ে পোঁটলা-পুঁটলি,ন্যাতা-কাঁথা,হাঁড়ি-পাতিল,উনুন-কড়াই নিয়ে শুরু হলো সেই দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা যেখানে প্রাণের ভয় নেই।শুনতে আশ্চর্য মনে হলেও এই হলো এক উদ্বাস্তু জীবনের গল্প যার অভিমুখ বারবার পালটেছে এখনো পাল্টাচ্ছে।
দেশভাগপ্রসূত দুই ভূখন্ড ভারত ও পাকিস্তান জন্মলগ্ন থেকেই বয়ে আসছে দেশভাগের ক্ষত।ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজন তথা সাম্প্রদায়িক বৈষম্যকে লালন করতেই যে ভাগাভাগি তা বাংলা কেটে পূর্ব পাকিস্তানের এবং পাঞ্জাব থেকে সিন্ধুপ্রদেশকে বিচ্ছিন্ন করে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্ম দিয়েছিল। এপার যখন ওপার হয়ে গেল,ভাতের হাঁড়ির চাল আর রুটির সাথে ডাল তখন অনিশ্চিত। সদ্য বেরনো শেকড় দিয়ে নতুন মাটি আঁকড়ে ধরতে মরিয়া মানুষ তার স্মৃতিতে লালন করেছে গোলা ভরা ধান-পুকুর ভরা মাছ আর ,সর্ষে ক্ষেতের হলুদ ফুলের স্বপ্ন।
দেশভাগের ফলে পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে দলে দলে মানুষ দিল্লী ও উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল।একই সাথে বাংলা ভাগ করে জন্ম নেয়া স্বাধীন ভারতের অন্যতম দোসর পাকিস্তানের অন্যতর ভূখণ্ড পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশ থেকে মানুষ ভারতে ঢুকে এলেন।পূর্ব ও মধ্যভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে শরণার্থী শিবিরে শুরু হল ইতিহাসের নতুন অধ্যায়।
“বাঙাল মানুষ নয়,অদ্ভুত জন্তু
লাফিয়ে সে গাছে ওঠে লেজ নাই কিন্তু”
অখণ্ড বাংলা ভেঙে জন্ম নিল পূর্ববঙ্গ আর পশ্চিমবঙ্গ।তেমনি বাঙালির মধ্যে খাদ্যাভ্যাস আর আঞ্চলিক পার্থক্য থেকে বাঙাল আর ঘটি এই দুই উপবিভাগের জন্ম হলো।বাঙালেরা ভিটে মাটি পুকুরের মাছ আমবাগান ছেড়ে যে দেশে এল সে দেশের ‘ঘটি’ বাঙালিরা তাদের রকম সকম দেখে এমনই অদ্ভুত ছড়া বানাতো।নতুন দেশে এসে অভাবের সংসারে সবার জন্য খাবারের সংকুলান করতে শাক-পাতা,উঠোনের ফালি জমিতে চাষ করা সবজি এসবেই ছিল মুশকিল আসান।রান্নার গুণে পলতা পাতার ঝোল,লাউয়ের খোসার চচ্চড়ি, আলুর খোসার বটি,কাঁচাকলার খোসা বাটা,ফুলকপির ডাঁটা চচ্চড়ি এসব পদ বাঙালির খাদ্যতালিকায় নতুন সংযোজিত হল।
“বাঙাল ইলিশ মাছের কাঙাল “
ভৌগলিক অবস্থানের বিচারে পূর্ববঙ্গকে ঘিরে রেখেছে নদী আর সমুদ্র। মাছ ব্যতীত বাঙালির অস্তিত্ব কল্পনাতীত।পদ্মা নদীর বিস্তীর্ণ পরিসরে ডিম পাড়তে আসা ইলিশ মাছের স্বাদ অন্য নদীতে আসা মাছের চেয়ে স্বতন্ত্র আর তাই এই মাছ বাঙালের আবেগ।কলকাতায় বা অন্য জেলায় পুনর্বাসিত মানুষ গঙ্গার ইলিশে মজতে পারে নি। ইলিশ মাছ রান্নায় পূর্ববঙ্গীয় ঘরানায় হরেক রকম কচু,কাঁচাকলা,কুমড়ো,চাল কুমড়ো এসবের ব্যবহার গঙ্গার ইলিশ রান্নায় এসে হারিয়ে গেল।ছিন্নমূল পরিবারে ইলিশ কিনে খাওয়া যখন বিলাসীতায় পরিণত হয়, তখন তা নিয়ে এত অনায়াসে সহজ ব্যঞ্জন রান্নার বদলে সর্ষে ইলিশের মতো রাজকীয় রান্নাই প্রাধান্য পেল।
পূর্ববাংলায় জলাভূমিতে অফুরান মাছ থাকার কারণে মাছ সরবরাহের কোন খামতি তো ছিলই না বরং উদ্বৃত্ত মাছ শুকিয়ে “শুঁটকি” বা শুকনো মাছ খাওয়ার প্রচলন ছিল।মূলত সমুদ্রের উপকূলের জেলা যেমন-খুলনা,চট্টগ্রাম বরিশাল ব্রক্ষ্মপুত্র তীরবর্তী সিলেট অঞ্চলে এর ব্যবহার জনপ্রিয় ছিল।পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এই সরলীকরণ করলেন যে বাঙাল মাত্রেই মেছো গন্ধের শুঁটকিপ্রেমী।
ভাত বাঙালির মূল খাদ্য। ভাতের চাল নিয়ে বরাবরই তারা সৌখিন।পুর্ববাংলার জলখাবারে আটা,ময়দার খাবারের পরিবর্তে ভাত বা ধান থেকে তৈরী হওয়া চিঁড়া-মুড়ি-খই খাওয়ার চল ছিল।দেশভাগের ফলে পূববাংলা থেকে আসা গোবিন্দভোগ, কাটারিভোগ,বালাম,চিনিগুড়া চালের ব্যবহার সীমিত হয়ে এল।পোলাও রান্নায় ছোট দানার সুগন্ধি আতপ চালের জায়গায় বাসমতী বা দেরাদুন সেই জায়গা নিল।ওদিকে পাকিস্তান থেকে সরবরাহ করা বাসমতী চাল পূর্ববঙ্গে সহজলভ্য হল।পূববাংলা থেকে আসা মানুষ ক্রমশ লুচি-পরোটার সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত হলেন।
“সেইবার যহন কইলকাতা আইলাম,একদিন নাইরকোল বাইট্যা চিনি দিয়া পাক দিয়ে ছাঁচে ফালাইয়া সন্দেশ বানাইসিলাম।দ্যাশ থেইক্যা আহনের সময় ছাঁচ কয়খান পোঁটলায় কইরা আনসিলাম।আমগোর গেরামে তো এইসব কিন্যা আনতে লাগত না তাই যতখুশি বানাইসি আর খাওয়াইসি।অহন তো সবই মাপা”।
এক নব্বই অতিক্রান্ত বৃদ্ধার স্মৃতিচারণ সূত্রে সহজেই অনুমেয় দেশভাগের পরে উদ্ভুত আর্থিক অনটনের পরিস্থিতি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আন্তরিক উদ্যোগের অভাব ছিল না।এভাবেই নারকোলের ছাপা সন্দেশ,কাটা নারকোলের নাড়ু, সাদা মালপোয়া পশ্চিম বাংলার খাদ্য সংস্কৃতিতে জায়গা করে নেয়। রাজশাহী,দিনাজপুর থেকে এ পারের মালদহ ও তার আশেপাশের অঞ্চলে আসা মিষ্টি ব্যবসায়ীদের হাতে নতুন করে তৈরী হয় বালুসাই,কানসাট,লাল চমচম,রসকদমের মতো মিষ্টি।লালমোহন রূপান্তরিত হয় পান্তুয়ায়,ছানামুখীর নবরূপে নাম হয় ছানার মুড়কি।নাটোরের কাঁচাগোল্লা,মুক্তাগাছার মন্ডা,কুমিল্লার মালাইকারি(চিংড়ির নয় ছানা আর ক্ষীরের) এসবের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হয় পশ্চিম বাংলার মিষ্টিপ্রেমী মানুষ।
মুঘল শাসকেদের সূত্রে দিল্লীতে যে শাহী মোগলাই খাবারের আধিপত্য ছিল তা ধীরে ধীরে সিন্ধুপ্রদেশ থেকে আসা তন্দুরীতে রান্না করা খাবার দখল করে নিল। মূলত রকমারি রুটি বানানোর জন্য ব্যবহৃত এই চুলা হিন্দু শরণার্থীদের মাধ্যমে দিল্লীতে আসে।১৯৪৭ সালে দরিয়াগঞ্জ অঞ্চলে দেশভাগের দাঙ্গায় ছাদ খসে পড়া,এক ভাঙা বাড়িতে কুন্দন লালা গুজরাল নামে পেশোয়ার থেকে আসা এক শরণার্থী তন্দুর বসিয়ে ‘মতি মহল’ নামে এক রেস্তোরাঁ শুরু করেন।এই তন্দুরী ছিল মধ্য এশিয়ায় প্রচলিত এক মাটির বড় আকারের চুলা যা মূলত রুটি তৈরীতে কাজে লাগত।মূলত নান আর মুর্গ তন্দুরী বিক্রি করে তিনি ব্যবসা শুরু করেন।কিন্তু সে সময়ে হিন্দু ও মুসলিম কোন সম্প্রদায়ের মানুষের কাছেই মুর্গীর তেমন গ্রহণযোগ্যতা ছিল না।তিনি অনুভব করেন ব্যবসা চালিয়ে যেতে হলে রুটি,ডাল মাখানির পাশাপাশি একটি ‘কারি’ প্রয়োজন।তাই উদ্বৃত্ত থেকে যাওয়া তন্দুরী মুর্গি দিয়ে দই-টম্যাটো-মাখনের ঘন থকথকে ঝোল দিয়ে কারি রান্না শুরু করেন এবং অল্পদিনেই তা বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেন। এই ‘মাখনি মুর্গ’ বা ‘চিকেন বাটার মশলা’ সমস্ত ভারতীয় খাবারের প্রতিনিধি হয়ে সসম্মানে এখনো রাজত্ব করে চলেছে।সময়ের সাথে হারিয়ে গেছে ‘গোলি কাবাব’, শাহজাহানাবাদ ঘরানার বিখ্যাত পোলাও,মীরাটের কুল্ফি ইত্যাদি। দিল্লী ছাড়াও লক্ষ্ণৌ ও আওয়াধ অঞ্চলেও এর অনিবার্য প্রভাবে মালাই পান, পসিন্দে, শামি কাবাব এমন অনেক পদ অপ্রচলিত হয়ে যায় কারণ এসব খাবারের গুণগ্রাহী ও রসদদার মুসলিম নবাব পরিবারসমূহ ততদিনে পাকিস্তানে পাড়ি দিয়েছেন। পরিবর্তে পাকিস্তান থেকে আগত পাচকের হাতের গুণে রেল স্টেশন লাগোয়া ধাবার “কালি মির্চ মুর্গ’ বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।
পাঞ্জাব থেকে মুম্বাই ও হায়দ্রাবাদে ছড়িয়ে পড়া শরণার্থীরা গড়ে তুলেছে “করাচি বেকারি”র মতো প্রতিষ্ঠান।এছাড়া মুম্বাইয়ের বিপুল জনপ্রিয় চাট,ভেলপুরি আসলে সিন্ধ্রী খাদ্যাভ্যাসের অবদান।দুপুরের খাবার আর রাতের খাবারের মাঝে খুচখাচ হাল্কা কিছু খাবার খাওয়ার যে অভ্যাস তা এভাবেই গড়ে ওঠে।সিন্ধ্রী ঘরানার আরেক অবদান মশলা পাঁপড়। দক্ষিণ ভারতের কিছু অঞ্চলে পাপ্পাদম নামে ডাল-চাল-সাবুর পাঁপড় প্রচলিত হলেও কয়েক রকম ডাল আর মসলা মিশিয়ে এই পাঁপড় খাওয়ার অভ্যাস দেশভাগের পরেই শুরু হয়।
খাদ্যাভ্যাসের উপর দেশভাগের উল্লেখযোগ্য এক প্রভাব হলো এই টম্যাটো-আদা-পেয়াঁজ-রসুনে জারিত যে কোন খাবারকেই একমাত্র ভারতীয় খাবার হিসেবে জাহির করা।বালতি মিট, কড়াই পনির আর মাখন মুর্গ ছাড়া ভারতীয় খাবার ভাবা যায় না আর মশলাদার পাঞ্জাবি খাবারই শুশুমাত্র ভারতীয় এই ধারণা ভেঙে বেরিয়ে আসতে প্রায় পঞ্চাশ বছর সময় কেটে গেছে।
দেশভাগ শুধু বয়ে আনা হাঁড়ি-কড়াই নয় তা সম্যক ভাবেই ফেলে আসা সুঘ্রাণ আর জিভের স্মৃতিও বটে।তাই বিশিষ্ট অধ্যাপক,নারীবাদী আন্দোলনের তাত্ত্বিক ও কর্মী কবিতা পাঞ্জাবি পাকিস্তানের শিকারপুরে গিয়ে অনুভব করেছিলেন তার আগের প্রজন্মের ছেড়ে আসা মাটির টান।সিন্ধ্রী পরিবারের সন্তান কবিতার শৈশবের স্মৃতি জুড়ে তার মামীর হাতে বানানো শিকারপুরী খোয়া, শীতকালে মায়ের তৈরী করা ফুলকপি-গাজরের আচার আর ঘিয়ে ভাজা আদা-রসুন-কাঁচালঙ্কা দিয়ে বানানো পরোটা ‘কোকি’,গরমকালে বেলফুলের ঠান্ডা শরবত “রাবেল” ফেলে আসা দেশের যে ছবি তার মনের ক্যানভাসে এঁকে দিয়েছিল তা যেন সত্যি হয়ে উঠেছিল সেদিন। পাঞ্জাবের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে যারা ভারতে এসেছিলেন তারা বিশ্বাস করতেন আর কখনো নিজের দেশে ফিরে যাওয়া হবে না।তাই এদেশেই নিজের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে দিয়ে গেছেন সেই দেশের স্বাদকোরকের আশ্বাস।ব্যবসায়িক বুদ্ধির যথার্থ প্রয়োগ নিজেদের ঘরানার খাবার জনপ্রিয় করে তুলেছেন।
দেশভাগ পরবর্তী সময়ে ভাগ্যান্বেষণে ইংল্যান্ডে বাঙালি ও পাঞ্জাবি শ্রমিক শ্রেণির মানুষের বিপুল সমাগমের হাত ধরে গড়ে ওঠে ভারতীয় খাবারের রেস্তোরাঁ যেখানে খেতে যাওয়ার রেস্ত রোজগারের ধান্ধায় ভিনদেশে যাওয়া খেটে খাওয়া মানুষের সাধারণত থাকত ।এসব দোকানের সূত্রে বর্তমানে বহুল প্রচলিত শব্দবন্ধ “Take Away” উদ্ভুত।গতরে খাটা কালো মানুষের দেশের ‘কারী’ দোকানে বসে খাওয়া ইংরেজ আভিজাত্য বিরুদ্ধ তাই এ হেন ব্যবস্থা।ভারত-পাকিস্তান-বাংলা-বিহার-গুজরাট-পাঞ্জাব যে অঞ্চলের খাবারই হোক না কেন তার নাম একটাই-কারী(curry)।এই হযবরল অভিধানে মাটন রোগানজোস,আলুর দম,পিন্ডি ছোলে,মুড়িঘণ্ট,ঝিঙে পোস্ত সবার নামই হিজবিজবিজ তথা ‘কারি। সাদা চামড়ার সাহেব ও বিবি যখন বুঝলেন এই কারি নামটা যথেষ্ট নয় তখন ১৯৭০ এর দশকে এল নতুন শব্দ- তন্দুর।আদতে যা একটি লোহা দিয়ে বানানো ভেতরের দেয়ালে মাটি লেপে নেয়া একটা বড়োসড়ো ড্রাম যা সাধারণত উত্তর উত্তর -পশ্চিম ভারতে দমে রান্না ও মসলা মাখানো মাংস পুড়িয়ে রান্না করার জন্য ব্যবহার করা হত।এভাবেই পালটে যেতে লাগল “ভারতীয়” খাবারের দোকানের নাম।পঞ্চাশের দশকে যা ছিল “রাজ বালতি “,ষাটের দশকে তাই হলো ‘ইন্ডিয়ান বালতি’।তারপর সত্তরের দশক হলো তন্দুরির দশক আর আটের দশকে ঔপনিবেশিকতা ভুত ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলতে চেয়ে “ভারতীয়” তথা মোগলাই খাবারের দোকানের নাম হলো “লাহৌর কড়াই”। অবশেষে নব্বইয়ের দশকের উদারীকরণ আর মুক্ত বাজার ও বাণিজ্যায়ণের পথ বেয়ে তাই হলো ‘জালেবি জাংশন’,’ক্যাফে লাজিজ’ ইত্যাদি।
“বুঝলা মা,আমার মা গরম ভাতের মইধ্যে সইরষা বাটা,কাঁসামরিস(কাঁচামরিচ) দিয়া ভাপে যেই ইলিশ মাছ রান্না করত,তার স্বাদ এহনো মুহে (মুখে) লাইগ্যা আছে”।
শ্বশুরমশাইয়ের এ হেন স্মৃতিচারণ শুনে বৌমা চেষ্টা করেছিল।কিন্তু একান্নবর্তী পরিবারের বিশাল মাপের ভাতের হাঁড়ি এখন বিলুপ্তপ্রায়।গোনাগাঁথা বর্গসংখ্যার সদস্যের সংসারে ইলিশ ভাপে খেতে তাই মাইক্রোওয়েভ আভেন বা প্রেসার কুকারের বাটিতেই ভরসা।তবু এর মধ্যে ফেলে আসা আনন্দ খুঁজে নেয়ার এক আন্তরিকতা আছে। ভুবনায়নের যুগে পৃথিবী যখন ছোট্ট একটা গ্রাম তখন দেশবিদেশের হরেক খাবার শুধুমাত্র অর্থের বিনিময়ে অনায়াসে হাতে পাওয়া এখন এক অভ্যাস মাত্র।কিন্তু খাবার তো শুধু উদরপুর্তির উপাদান নয়,যে স্বাদ,আঘ্রাণ,নিরাপদ নির্লিপ্তি, তৃপ্তির আশ্বাস নিজের পরিবারে রান্না করা খাবারে মিশে থাকে তা কোন মূল্যেই কেন যায় না।তাই হারিয়ে যায় এমন অনেক কিছু হারানো বাস্তুভিটার মতো যা আর ফিরে পাওয়া যায় না।